পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের অসাধারণ সুন্দর একটি অংশ। সমগ্র দেশের একমাত্র পাহাড় বিধৌত অঞ্চলটির আয়তন দেশের মোট আয়তনের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। এর মধ্যে রাঙ্গামাটি আয়তনের দিক দিয়ে গোটা দেশের মধ্যে বৃহত্তম জেলা। শুধুই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, অফুরন্ত বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ এই অঞ্চল খনিজ সম্পদেরও আধার। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনেও এই অঞ্চল যথেষ্ঠ গুরুত্বের দাবী রাখে। এই এলাকার অশান্ত পরিস্থতির কথা কারও অজানা নয়, আজও চলছে সেসব।
পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ
একটি সাম্প্রতিক জরিপ হতে দেখা যায়, এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭%-৪৯% বাঙালি, বাকি ৫৩%-৫১% উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে ‘চাকমা’ গোষ্ঠিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৩৩% (প্রায়) হচ্ছে চাকমা জনগোষ্ঠি। এছাড়া অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মারমা, ত্রিপুরা, তংচংগ্যা, পাংখো, মুরং, বোম, কুকি, গারো, খিয়াং, চাক, লুসাই, খুমি ইত্যাদি উল্ল্যেখযোগ্য। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় চাকমাদের আরাকান থেকে বিতাড়িত করে মগরা। আসামের নৃতাত্ত্বিক তথ্যের পরিচালক মি.জে পি মিলস-এর মতে চাকমারা সেখান থেকে আশ্রয় নেয় কক্সবাজার এলাকায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে ১৮ শতাব্দীতে।
উপজাতীয় রাজাদের বংশক্রম থেকে দেখা যায়, চাকমাদের মধ্যে অনেক রাজাই মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তাঁরা মুসলিম নাম ও পদবি গ্রহন করতেন। এছাড়া তাঁদের সাথে মুসলিম বিবাহ-রীতির হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া গেছে অপর একটি গবেষনায়। চাকমাদের ধর্ম বৌদ্ধ হলেও, ধর্মগত আচারে বৌদ্ধত্বের বিশেষ প্রমান পাওয়া যায় না। ১৮ শতকে বহু চাকমার মুসলিম হবার প্রমান রয়েছে। পরে আবার হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে।
সর্বপ্রথম ব্রিটিশ আমলেই কালিন্দি রানী নামের তাঁদের এক রানী সকলকে বৌদ্ধ হবার নির্দেশ দেন। ১৮ শতাব্দীতে তাঁদের মধ্যে এতটাই বাঙালিয়ানা ভর করে যে, জে পি মিলস বলেন, 'এরা আচারে-ব্যাবহারে ও সংস্কৃতিগত বিষয়ে খুবই বাঙালি হয়ে গেছে (Most Bangalaised tribes)'। আরেকটি গবেষনায় দেখা গেছে, চাকমা ভাষা বাংলা ভাষার একটি উপভাষা। এমনকি হুমায়ুন আজাদের মতে চাকমা রাজা মোআন তসনি ব্রহ্মদেশ হতে তাড়া খেয়ে ১৪১৮ সালে কক্সবাজারের টেকনাফ ও রামুতে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে।......। তারপর, পালাক্রমে মারমারা আসতে শুরু করে এবং একটা সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপী বসতি ছড়িয়ে পড়ে। জে পি মিলসের মতে, এই ‘একটা সময়’ হচ্ছে ১৮ শতাব্দী (সুবোধ ঘোষ)। সুতরাং, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা সহ অধিকাংশ উপজাতিদের বসবাসের ইতিহাস বড়জোর ২০০-৩০০ বছর। বাঙালি ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ও বসবাসের ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায় উপজাতিরা আদিবাসী নয়। কিন্তু কেন ইদানিং আদিবাসী বনে যাবার জন্য তাঁদের এত দৌড়ঝাঁপ? কেন এখন ‘উপজাতি’ শব্দটায় তাঁদের এত এলার্জি, কেন তাঁরা এই শব্দটির দরুন 'অপমানিত' বোধ করেন, যেখানে তাঁরা এমনকি ‘৯৭ সালে করা শান্তিচুক্তিতেও নিজেদের উপজাতি হিসেবেই নিজেদের উপস্থাপন করেছেন?
পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমিয়াদের সংগ্রামের সূচনাঃ
পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন হিসেবে শান্তিবাহিনীর উদ্ভবের পটভূমি রচিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়ি জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। মূলত ১৯৫৭ সালে কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধের কার্যক্রম শুরু হয়। এর কারণে বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি, আবাদি জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ অবশ্য এসকল জমির প্রকৃত মালিক ছিল না, কারণ তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল অনুসারে এলাকার সব জমিই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। তথাপি মানবিক কারণে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্থদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। লেকের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ ৩৩.২২ মিটার উঁচু পর্যন্ত এলাকাসমুহ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। মূল লেকটির আয়তন প্রায় ১৭২২ বর্গ কিমি, তবে আশপাশের আরও প্রায় ৭৭৭ বর্গ কিমি এলাকাও প্লাবিত হয়। কাপ্তাই বাঁধের কারণে আনুমানিক ১৮,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৫৪ হাজার একর কৃষিজমি পানিতে তলিয়ে যায় এবং প্রায় ৬৯০ বর্গ কিমি বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেসময় ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। তারপরও অসন্তোষ থেকে যায়।
ওই অসন্তোষেরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আত্মপ্রকাশ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির। এর আশু কারণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উদ্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা নিজেদের জুমিয়া জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে এর স্বীকৃতি দাবি করে। স্বীকৃতিলাভে ব্যর্থ হয়ে জুমিয়া জাতি আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৪ দফা দাবিনামা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট পেশ করে:
(ক) নিজস্ব আইন পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা।
(খ) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যাদেশের ‘হিল ম্যানুয়েল অ্যাক্ট’ বাংলাদেশের সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা।
(গ) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা এবং
(ঘ) সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষিত রাখার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
এই দাবিসমূহের আলোকে ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা লিখিতভাবে সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবি জানান। কিন্তু নতুন সংবিধান পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মর্যাদা দেয় নি। এরূপে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।
কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে শান্তিবাহিনী তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে। প্রতিটি অঞ্চলকে আবার ৩টি সেক্টরে এবং সেক্টরগুলোকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয়। জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার দুর্গম অরণ্যে। ১৯৭৪ সাল নাগাদ বিপুল সংখ্যক পাহাড়িদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে শান্তিবাহিনীভুক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়ে মিলিশিয়া বাহিনী গঠিত হয়। শান্তিবাহিনী ও মিলিশিয়া বাহিনীকে সহায়তার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বহুসংখ্যক যুব সমিতি ও মহিলা সমিতি গড়ে তোলা হয়। সামগ্রিক প্রস্ত্ততি গ্রহণ শেষে শান্তিবাহিনী ১৯৭৬ সালের প্রথমদিকে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। শান্তিবাহিনী পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী বাঙালিদের আক্রমণ ও হত্যা, নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণ, তাদের মতাদর্শ বিরোধী উপজাতীয়দের হত্যা, সরকারি সম্পদের ক্ষতিসাধন, অপহরণ ও বলপূর্বক চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ জোরদার করে। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর অন্তর্দলীয় কোন্দলে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন।
মানবেন্দ্র লারমার হত্যাকান্ডের পর শান্তিবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে (লারমা ও প্রীতি গ্রুপ) আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিয়ে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় এবং তাদের প্রতি অস্ত্র সমর্পণ ও বিদ্রোহ সংঘাত বন্ধ করার আহবান জানায়। প্রীতি গ্রুপের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু লারমা গ্রুপ নাশকতামূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। ইতোমধ্যে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার বোধিপ্রিয় লারমা জনসংহতি সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন (১৯৮৫)। এরপর বিভিন্ন সময়ে সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত সরকার পূর্ববর্তী সকল সরকারের নেয়া শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। অবশেষে পরবর্তী মেয়াদের (১৯৯৬-৯৭) জন্য নির্ধারিত সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৯ সালে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ মহাসম্মেলনে শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।
শান্তিবাহিনীর নৃশংসতাঃ
হুমায়ুন আজাদ শান্তিবাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের ভয়াল আক্রমনের শিকার হন নীরিহ বাঙালিরা। এ ছাড়াও তাঁরা হত্যা করে সেনাবাহিনীর সহযোগী পাহাড়িদের, অপহরন করে বাঙালি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যাবসায়ীদের। ১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারী তাঁর অপহরন করে শেল তেল কোম্পানির কাজে নিয়োজিত ৫ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে। বিপুল মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে পরে ছাড়িয়ে আনা হয়। '৯৭ সালে থানচির থানা নির্বাহীকে অপহরণ করে মুক্তিপন দাবী করে তাঁরা। সেনাবাহিনী মুক্তিপন ছাড়াই উদ্ধার করে তাকে। সেতু ধ্বংস করে, বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন করে এবং সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাঁধিয়ে উপজাতিদের শরণার্থীরূপে ভারত যেতে বাধ্য করে শান্তিবাহিনী। এ সময় উল্লেখযোগ্য সহিংসতার মধ্যে ছিল '৯৬ সালে ২৯ কাঠুরিয়াকে হত্যা, ভূবনছড়া গনহত্যা, ইত্যাদি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত শান্তিবাহিনী ৯৫২ জন বাঙালি ও ১৮৮ জন পাহাড়িকে হত্যা, ৬২৬ জন বাঙালি ও ১৫২ জন পাহাড়িকে জখম এবং ৪১১ জন বাঙালি ও ২০৫ জন পাহাড়িকে অপহরণ করে। এই তথ্য জানিয়েছেন, M R Shelly ১৯৯১ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : An Untold Story’ বইতে। হুমায়ুন আজাদ কতৃক প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী '৯৭ সাল পর্যন্ত এই হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ- ১৭ জন সৈনিক, ৯৬ জন বিডিআর, ৪১ জন পুলিশ, অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৫ জন। আহত হয়েছে মোট ৩৭৩ জন, ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫৬ জন। অসামরিক ব্যাক্তিরাই মরেছে বেশি- বাঙালি ১০৫৪ জন, উপজাতীয় ২৭৩ জন। আহত হয়েছে- ৫৮৭ জন বাঙালি, ১৮১ জন পাহাড়ি। অপহৃত হয়েছে- ৪৬১ জন বাঙালি আর ২৮০ জন উপজাতীয়।
শান্তিচুক্তির ব্যবচ্ছেদ
অশান্ত পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে তৎকালীন আওয়ামী সরকার শান্তিচুক্তির আয়োজন করে। মূলত দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রায় কোণঠাসা করে ফেলার পর বিদেশীদের চাপে এদের নির্মূল না করে শান্তিচুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। চুক্তির বেসিক বিষয় ছিল সন্তু লারমা নেতৃত্বে শান্তি বাহিনী অস্ত্রসমর্পন করবে। বিনিময়ে সরকার তাদের ক্ষমা করে দিবে এবং তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সেজন্য তাদের টাকা ও সম্পদ দিয়ে পূনর্বাসন করা হবে। চুক্তিটি উপজাতি বা জুমিয়াদের পক্ষেই গিয়েছে। অউপজাতি তথা বাঙ্গালীদের অধিকার ক্ষণ্ণ করা হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু ধারা সেখানে সংযুক্ত হয়েছে যা বাংলাদেশ সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্রের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ।
শান্তি চুক্তিতে আপাত স্থিতিশীলতা আসলেও, এর অসারতা এখন বোঝা যাচ্ছে। এখনও পাহাড়ে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যায়। প্রায় প্রতি সপ্তাহে জনসংহতি ও চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর মধ্যে চাঁদাবাজি সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বন্দুক যুদ্ধ ঘটে। সেখানকার পাহাড়ি-বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছে আতংকে। প্রায়ই বাঙালি-পাহাড়ি দাঙ্গায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়। চাঁদাবাজি, খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস আগের চেয়ে তো কমেইনি, বরং তিনগুণ বেড়েছে। কারণ জেএসএস(জনসংহতি), ইউপিডিএফ ছাড়াও জেএসএস থেকে ‘সংস্কারপন্থী’ বলে পরিচিত নতুন আরেক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে। এবার সমপরিমাণ চাঁদা তিন দলকেই দিতে হয় পাহাড়ি-বাঙালি সবাইকে। এ ছাড়া চুক্তি বাস্তবায়নের পরপরই বাঙালিরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের আপত্তির কথা তীব্রভাবে তুলে ধরে। সে গুলো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হল-
১- চুক্তির খ-খণ্ডের ৩০-এর ঘ- ধারা মোতাবেক বাঙালিদের নাগরিকত্ব সনদ দিবেন উপজাতীয় রাজা এমনকি নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলেও, যা সংবিধানসম্মত নয়।
২- চুক্তির খ- খণ্ডের ২৬ ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমতি ব্যাতীত জমি-ভূমি ক্রয়বিক্রয়য়, হস্তান্তর এমনকি ইজারা পর্যন্ত দিতে পারবে না কেউ, স্বয়ং সরকারও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে বঞ্চিত করা হয়েছে বাঙালিদের।
৩- পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যপদ সহ গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্ব উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, অথচ সেখানে বাঙালিদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকেরও বেশী।
৪- চুক্তির খ-খন্ডের ১৬ ধারায়, যে শান্তি বাহিনী দীর্ঘ এত ২৪ বছর ধরে দেশপ্রেমিক বাঙালি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করে আসছে, তাদেরকে ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার সহ পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। অথচ দেশমাতৃকার জন্য শান্তি বাহিনীর হাতে যারা নির্মমভাবে আহত/নিহত হয়েছে, তাঁদেরকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করা হয়নি।
৫- চুক্তির গ-খন্ডের ৭ নং ধারা মোতাবেক পরিষদ সমূহের তিনটি উপসচিব ও একটি যুগ্ন-সচিব সহ চারটি পদে বাঙালি হওয়ার অপরাধে বাঙালি কর্মকর্তাদের বদলে পাহাড়িদের নিয়োগ দেয়া হবে, এর ফলে বাঙালিদের ন্যায্য প্রাপ্তির জন্য আর কোনও প্রশাসনিক স্তর রইলো না।
৬- চুক্তির খ-খণ্ডের ৩২ ধারায় পরিষদসমূহের ধারায় মহান জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের বিরুদ্ধে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধানসম্মত হতে পারে না। এ যেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থার ভেতর আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র।
৭- চুক্তির খ- খণ্ডের ২৪ ধারায় সিপাই থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত পদে শান্তি বাহিনী প্রত্যাগতদের নিয়োগের ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। যারা কিছুদিন আগেও আনসার, বিডিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনী সহ সাধারণ বাঙালিদের দেখা মাত্র গুলি করতো, তাঁরা এবার বৈধ অস্ত্র দিয়ে তা করতে যে দ্বিধা করবে না, তাঁর নিশ্চয়তা কি?
৮- চুক্তির খ-খন্ডের ১৪ ধারা অনুযায়ী পরিষদকে সরকারী কর্মচারী উপজাতীয় থেকে নিয়োগ, বদলি ও শাস্তি প্রদান ইত্যাদি ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে।
৯- চুক্তির খ খণ্ডের ২৬ ধারায় (গ) অনুযায়ী চেইনম্যান, আমিন, সারভেয়ার, কানুনগো, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সন্তু লারমা কতৃক নিয়ন্ত্রিত (এখন পর্যন্ত সন্তু লারমাই সেটার চেয়ারম্যান, অজ্ঞাত কারণে নির্বাচন হয়নি একবারও) আঞ্চলিক পরিষদকেই দেয়া হয়েছে। এর কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা নিজেদের ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন।
১০- চুক্তির গ-খন্ডের ৮ ধারায় পৌরসভা, স্থানীয় বিভিন্ন পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব পরিষদকে দেওয়া হয়েছে, যা প্রজাতন্ত্রের ভেতর আরেকটি প্রজাতন্ত্র ও ইউনিটারি বাংলাদেশ কনসেপ্টের সাথে সাংঘর্ষিক।
১১- চুক্তির ৭ ধারা ও ১৬ ধারার (ঘ) অনুযায়ী শান্তি বাহিনী ও উপজাতিরা এ যাবতকাল যত ব্যাংক ঋণ নিয়েছে, তা সুদ সমেত মওকুফ করা হয়েছে। অথচ, যে সকল বাঙালি শান্তি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কারণে ঋণ নিয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি, পারলেও শান্তি বাহিনী তা ধ্বংস করে দিয়েছে, তাঁদের ঋণ মওকুফ করা হয়নি, বরং সার্টিফিকেট মামলায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
১২- বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের এবং ২৮ (১, ২, ৩) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে ও পশ্চাৎপদ জনগণের (পাহাড়ি) ধোঁয়া তুলে চুক্তির বৈধতার সাফাই দেওয়া হচ্ছে। যদি ঐ ধারার প্রয়োগ করতেই হয়, তাহলে সেটির সুযোগ তো চাকমারা পেতে পারে না। কেননা, চাকমাদের মধ্যে ৭০% শিক্ষিত, বাঙালিরা ১০%, অন্যান্য উপজাতিরা ১০%-১২% এর বেশি নয়। চাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিকভাবে চাকমারা এগিয়ে। সে ক্ষেত্রে ‘পশ্চাৎপদ অংশ’ তো বাঙালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিরা। তাছাড়া একই পাহাড়ে, একই আবহাওয়ায়, একই প্রতিকূল অবস্থায় বাঙালিরাও তো বাস করছে। সুতরাং, পশ্চাৎপদ অংশের উন্নয়নের নামে চাকমাদের উন্নয়ন নয়, বরং পার্বত্য বাঙালি ও ক্ষুদে উপজাতিদের উন্নয়নে সংবিধানে উল্লেখিত ধারা প্রয়োগ ও চুক্তি করা উচিত ছিল।
দিন দিন বাঙ্গালীদের বঞ্চনা ও উপজাতীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি একই রাষ্ট্রের দুই নীতিকে প্রকট করে তুলছে। যা সামাজিক ভারসাম্যে নিদারুন ক্ষতি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা শান্তি চুক্তিকে নিজেদের প্রতিকূলে ভেবে নিয়েছে। সেই বিষয়টি ও বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা কি যৌক্তিক নয় যে, শান্তি চুক্তি নতুন এক অশান্তির বীজ বপন করেছে? আহমদ ছফা শান্তি চুক্তি নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, ‘পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে এমন কিছু বিস্ফোরক উপাদান আছে, যা উপজাতি-অউপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির পরিমাণ বাড়াবে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং নানা অংশে ছড়িয়ে দেবে অশান্তির আগুন’। আজ আমরা তাঁর কথার আক্ষরিক ফলে যাওয়া দেখতে পাই।
উপজাতিদের রাতারাতি আদিবাসী হয়ে যাওয়াঃ
চাকমা-মারমারা নিজেদের উপজাতি হিসেবেই প্রকাশ করতো। ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও সন্তু লারমা নিজেকে উপজাতি পরিচয়েই পরিচিত করিয়েছিলেন। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বাংলাদেশে আদিবাসী বিষয়ক প্রচারণার বেসিক পার্সন। জনসংহতি সমিতি ও সন্ত্রাসী সংগঠন শান্তি বাহিনীর নেতা সন্তু লারমাও শুরুতে আদিবাসী দাবির পক্ষে ছিলেন না। দেবাশীষ রায়ের দাবি বলে তিনি এর সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিদেশী রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থার সমর্থন এবং আর্থিক প্রলোভনে তিনি এই দাবিতে শরিক হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি।
বিশ্ব আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে আবার নতুন করে বিতর্কটি জমে উঠেছে। বাংলাদেশে আদিবাসী কারা- এই বিতর্কটি খুব বেশী হলে এক দশকের। বিষয়টি নতুন হলেও তা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সচেতন মহলকে বেশ আন্দোলিত করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে এ বিতর্কের সমাধান অবিশ্যম্ভাবী।
২০১৪ সালের ৭ আগস্ট জারী করা সরকারি এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে দেশে আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও বিভিন্ন সময় বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে ‘আদিবাসী’ শব্দটি বারবার ব্যবহার হয়ে থাকে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, “আগামী ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আলোচনা ও টকশোতে ‘আদিবাসী’ শব্দটির ব্যবহার পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং সকল আলোচনা ও টকশোতে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকসহ সুশীল সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার পরিহারের জন্য পূর্বেই সচেতন থাকতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।”
কিন্তু বেশিরভাগ গণমাধ্যম ও গণমাধ্যম ব্যক্তিগণকে আগের মতই দেদারছে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিশেষ করে যে সরকার এই পরিপত্র জারি করে সেই সরকারেরই অনেক মন্ত্রী, এমপিসহ ঊর্ধ্বতন পদাধিকারিকগণ এই পরিপত্র অবজ্ঞা করে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উপজাতি সম্প্রদায়গুলোকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে তারা সরকারি পরিপত্রের তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থপুষ্ট ও মদদপুষ্ট বিতর্কিত সিএইচটি কমিশন উপজাতিদের আদিবাসী হিসেবে চালিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে বহু বছর জুড়ে। সাম্প্রতিক কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনায় এই কমিশনের প্রত্যক্ষ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছে। শান্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিতেই মূলত সিএইচটি কমিশন কাজ করে গেছে। শান্তিচুক্তি হবার পর, হঠাত বেকার হয়ে পড়ে এই কমিশন। অনেকেই বলে থাকেন ফান্ডিং-এর অভাবই ছিল এর মূল কারণ। এরপর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না – এই মর্মে আবার গঠিত হয় এই কমিশন। এবার সুলতানা কামাল, ইফতিখারুজ্জামান, জাফর ইকবাল, কামাল হোসেন সহ অনেক বাংলাদেশী এই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হন। এর প্রধান হিসেবে অবশ্য একজন বৃটিশ সংসদ সদস্য দায়িত্ব লাভ করেন, তিনি খৃষ্টান পাদ্রি লর্ড এরিক অ্যামভুরি। এটা খুব সাধারণ কথা এই কমিশন যতটা না বাংলাদেশ বা উপজাতিদের স্বার্থ দেখবে তার চাইতে বেশী দেখবে আমেরিকার স্বার্থ। এবং সেটাই তারা করে যাচ্ছে সফলভাবে। ইতিমধ্যে তারা উপজাতিদের আদিবাসী হিসেবে প্রচার করার যাবতীয় পন্থা ব্যবহার করেছে। এই বিষয়ে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখছে ডেইলী স্টার, প্রথম আলো গং। যেখানে এই কমিশনের কাজ হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয় নিয়ে কাজ করা সেখানে তারা কিভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের অধিকার হরণ করা যায়, সেই চেষ্টায় লিপ্ত। বাঙ্গালী উচ্ছেদ ও বাঙ্গালীদের সুযোগ সুবিধা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করে তারা রিপোর্ট দিচ্ছে।
তারা হঠাৎ উপজাতিদের আদিবাসী বানাতে চাচ্ছে কারণ বাংলাদেশ সরকার যদি কোনভাবে উপজাতিদের আদিবাসী স্বীকৃতি দেয় তাহলে জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের স্বায়ত্বশাসনের নাম করে খুব সহজেই স্বাধীন করে দিতে পারবে। যে ধারার ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘ ও আমেরিকা 'আদিবাসী' পরিচিতি আদায়ের জোর চেষ্টা করছে। সেটি নিন্মরুপ-
আদিবাসীদের অধিকারের উপর জাতিসঙ্ঘের ঘোষণাপত্র : ধারা ৩
"United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:
Article 3 -- Right to Self-determination
Article 3 -- Right to Self-determination Indigenous peoples have the right of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."
ধারা ৩ -- আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে। এই অধিকারের বলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে (অর্থাৎ তারা কি কোন দেশের মধ্যে থাকবে, না সেই দেশ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন দেশ গঠন করবে -- সেটা তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে, যেমন জুমিয়ারা কি বাংলাদেশের মধ্যে থাকবে, না বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড গঠন করবে তা জুমিয়াদের রাজনৈতিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে) এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অনুসরণ করবে।
এই ধারার আলোকেই বিনা রক্তপাতে পশ্চিমা দেশগুলো ও জাতীসংঘের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সম্প্রতি সময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে পূর্বতীমুর। যা অখন্ড ইন্দোনেশিয়ার অঞ্চল ছিলো। 'আদিবাসী' শব্দ চর্চার বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করেই এক শ্রেনীর মানুষ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দক্ষিণ এশীয় এজেন্ট হিসেবে এদেশে সক্রিয় বলে ব্যাপক সন্দেহের আর কোন অবকাশ নাই।
আমেরিকার স্বার্থ কি?
সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর চীন ধীরে ধীরে বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজকে প্রস্তুত করছে। এমতাবস্থায় চীনকে যদি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সবচেয়ে যোগ্যতম স্থান হচ্ছে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা কেননা এখানে চীনের সাথে আছে জনসংখ্যার মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক মিল এবং কম দূরত্ব। এমতাবস্থায় চীন এই এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এটা কোন দিক থেকে গ্রহণ করবে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশের সরকারযন্ত্রের, সামান্য ভুলে কারণে হয়তো এই সম্ভাব্য এলাকাটি এক সময় সমগ্র জাতির দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
কেন আমেরিকা উপজাতিদের স্বাধীন করতে ভূমিকা রাখবে, এই প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল বিভাগের গবেষক জনাব কাজী বরকত আলী। তিনি বলেন একটা প্রমাণ সাইজের বিশ্ব মানচিত্র নিয়ে তার মধ্যে দুই ইঞ্চি ব্যসের অনেকগুলো বৃত্ত একটা আরেকটাকে স্পর্শ করে যদি আঁকেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, প্রতিটা বৃত্তের মধ্যেই আমেরিকান ঘাঁটি রয়েছে। শুধু ব্যতিক্রম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃত্তদ্বয়। আর এই বৃত্তের মধ্যেই রয়েছে দু'দুটো পরাশক্তি ভারত ও চীন। এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এখানে একটা ঘাঁটি খুব প্রয়োজন আমেরিকার।
এখানে দুটো পরিকল্পনাকে আবর্তিত হচ্ছে তাদের কার্যক্রম। প্রথমত উপজাতি জুমিয়াদের আদিবাসী স্বীকৃতি আদায় করে সেখানে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আলাদা স্বায়ত্বশাসন বা আলাদা রাষ্ট্র করার মাধ্যমে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত কোন কারণে সেটি সম্ভব না হলে এই অঞ্চলের অধিকাংশ গরিব উপজাতিদের সচ্চল জীবনের লোভ দেখিয়ে খ্রীস্টান বানিয়ে তাদের মাধ্যেমে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করা। সেই লক্ষ্যে এখন অনেকদূর তারা পৌঁছে গিয়েছে।
যে উপজাতিরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে ওদের নিয়ন্ত্রনে একটা রাষ্ট্র গঠনের স্বপন দেখছে যদি আমেরিকার কূটচাল বাস্তবায়িত হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হবে উপজাতিরাই। আর আমাদের দেশ হবে খন্ডিত। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হবে লঙ্গিত। আরো জঘন্য ব্যাপার হল, আল্লাহ না করুন যদি আমেরিকার কূটচাল বাস্তবায়িত হয় তাহলে বিষয়টা মোটেই ভালোভাবে নিবেনা চীন ও ভারত। সেক্ষেত্রে তারা (ভারত ও চীন) প্রতিহত করার জন্য যেকোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না। তখন বাংলাদেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। যারা যুদ্ধ করবে তারা এখানে যুদ্ধ করতে মোটেই দ্বিধা করবে না কারণ এখানে তাদের জনগণ নেই।
তাই সকলে সচেতন থাকুন। দেশদ্রোহী সুলতানা কামালের সিএইচটি কমিশন ও প্রথম আলো গংদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এখনই সময় প্রতিরোধের। এদেশে আমরাই আদিবাসী। আমাদের রয়েছে সুদীর্ঘ চার হাজারেরও বেশী বছরের ইতিহাস। এই অঞ্চলে বাঙ্গালীদের আগে আর কোন জাতি ছিল বলে কোন ইতিহাস নেই। আমরাই এই অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাই আমাদের দেশকে আমরাই রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। আবার এর মানে এই নয় যে আমরা উপজাতিদের উচ্ছেদ করতে চাই। উপজাতিরা যেভাবেই হোক আমাদের দেশে এসেছে। আমাদের দেশের নাগরিক। আমাদের এই পর্যায়ে এসে জাতিগত বিভেদ করে আমরা আমাদের দেশকে হুমকির সম্মুখিন করতে চাই না। আমাদের বাঙ্গালী, চাকমা, মারমা, উপজাতি-অউপজাতি এসব পরিচয়ের চাইতে বড় পরিচয় হলো আমরা বাংলাদেশী। আমরা সবাই মিলে এদেশের জন্য কাজ করবো, এখানে সবার অধিকার সমান হবে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা আমদের সহায় হোন।

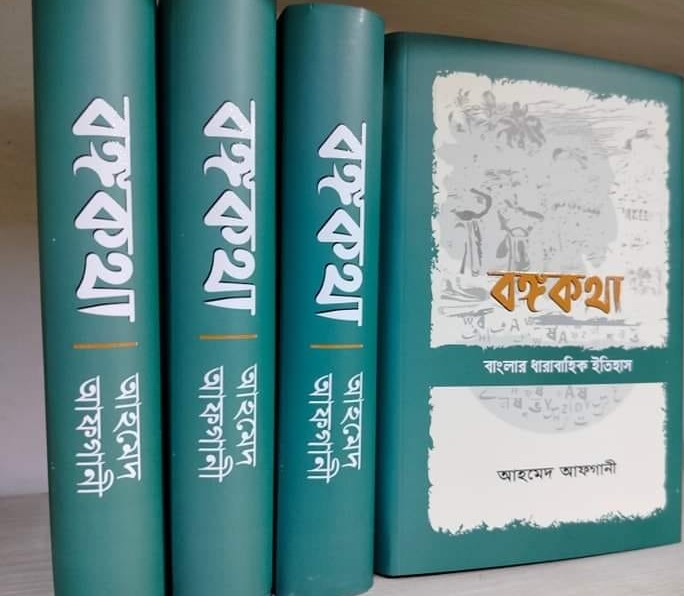





একসাথে অনেক কিছু জানলাম...
উত্তরমুছুনধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে।
আপনাকেও ধন্যবাদ ভাই
উত্তরমুছুনএই মন্তব্যটি লেখক দ্বারা সরানো হয়েছে।
উত্তরমুছুন