বাংলাদেশে ৫০ বছরে এই পর্যন্ত ৭১ এর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে ভালো কোনো তালিকা বা রেকর্ড তৈরি করেনি এদেশের কোনো সরকার। বরং পারলে বাধা দিয়েছে। মুজিব সরকার কমিটি গঠন করে পরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে যারাই ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছেন তারা খুন হয়েছেন। এই ধারাবাহিক খুনের সর্বশেষ শিকার জাতীয় ভার্সিটির ভিসি আফতাব আহমাদ। তাই আজ পর্যন্ত সুষ্ঠু কোনো শুমারি হয়নি যে, কতজন মানুষ ১৯৭১-এ খুন হয়েছেন।
২০১০ সালে সংসদে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা গণনার কোন পরিকল্পনা এ সরকারের নেই'। বিদেশের অনেক ব্যক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য দিলেও দেশের সব সরকার ছিল বরাবরের মতই নির্বিকার। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৯৭২ সনের ১০ জানুয়ারী ভারতের পালাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে; আজোবধি ৩ (তিন) মিলিয়ন তথা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এ সংখ্যাই প্রচলিত আছে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে বের হয়ে দেশে না আসতেই কোনো তদন্ত ছাড়াই কেন এমন বললেন এই বিষয়ে বিবিসি সাংবাদিক সিরাজুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশে ফেরত আসার সময় মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন কেমন মানুষ মারা গেল যুদ্ধে? তখন সিরাজুর রহমান তাকে জানিয়েছেন আমরা আশংকা করছি প্রায় তিন লক্ষ মারা গেছে। এরপর সাংবাদিকদের তিনি থ্রি মিলিয়ন বলেছেন। সিরাজুর রহমান বলেছেন সেই সময়ের উত্তেজনা ও উদ্ভ্রান্ত মুহূর্তে শেখ মুজিব তিন লক্ষকে ভুলে থ্রি মিলিয়ন বলে ফেলেছেন।
বাংলাদেশে সেই সময় মুজিবকে তার অনুসারীরা প্রফেটিক মর্যাদা দিয়েছে। মুজিব বলেছে অতএব তাই ঠিক! এমন অবস্থা আজো চলমান। এ ব্যাপারে ১৫.০৬. ১৯৯৩ তারিখে সংসদে আলোচনায় কর্ণেল আকবর হোসেন বলেন যে, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে উল্লেখ করে যা মূলতঃ প্রকৃত সংখ্যার ১০ (দশ) গুণ। তখন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ বলেন যে, জিয়াউর রহমানসহ কেউ এ সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করেননি; আমাদের নেতা শেখ মুজিব যেহেতু সংখ্যাটি বলেছেন ধরে নিতে হবে এটিই সঠিক।
শর্মিলা বসু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে সে হিসেব দিতে গিয়ে শাখারীবাজারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে“ In Shakharipara an estimated 8,000 men, women and children were killed when the army, having blocked both ends of winding street, hunting them down house by house. The description is entirely false. Survivors of the attack on Shakharipara on March 26 testify that about 14 men and one child (carried by his father) were killed inside a single house that day."
বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে এই সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার, শর্মিলা বসু বলেন এ যুদ্ধে প্রায় ৩৬ হাজার নিহত হয়েছেন, কল্যাণ চৌধুরীর মতে ১২,৪৭,০০০ জন এবং British Medical Journal এ প্রকাশিত “Fifty Years of Violent War Deaths from Vietnam to Bosnia: Analysis of Data from World Health Survey Programme” বলা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২,৬৯,০০০ (দু' লক্ষ ঊনসত্তর হাজার) জন মানুষ মারা গিয়েছে। এভাবে নানান বর্ণনা পাওয়া যায়। বাঙালি লেখকরা প্রায় সবাই মুজিবের কথাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে নিহতের সংখ্যা তিরিশ লাখ উল্লেখ করেছেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ টিভি ভাষণে বলেন, “দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।
শেখ মুজিব ২৯ জানুয়ারী ১৯৭২ ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ আব্দুর রহিমকে প্রধান করে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। ৩০ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা, ক্ষয়-ক্ষতিসহ এর সাথে জড়িতদের অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কমিটিকে পরে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত এই আব্দুর রহীমকে প্রধান করেই রাজাকারে বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শেখ মুজিব সরকার প্রধান রাজাকার কমান্ডার আব্দুর রহীমকে সচিব পদে উন্নীত করেন।
বস্তুত ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫ মার্চ আওয়ামী ও নিউক্লিয়াসের সন্ত্রাসীদের চালানো বর্বরতার একটি গোপন ঘাঁটি ছিল সেই বাড়িটি। যেখানে সন্ত্রাসীরা একত্রিত হতো এবং এখানে অস্ত্র ও বোমা বানানো হতো। সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় তারা সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে মারা যায়। এই সংখ্যা ১৫। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতকারীরা সংখ্যা দেখিয়েছে ৮০০০। শাঁখারিবাজারে সব বাড়িতে গণহারে অভিযান চালানো হয় নি, শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হন। যেভাবে ঢাবির সব হলে অভিযান চালানো হয়নি। শুধুমাত্র দুটি হলে অভিযান চালানো হয়েছে।
শর্মিলা বসু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে তিনি একজন নিরপেক্ষ গবেষক বলে বিবেচিত। তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যা প্রমাণ করতে এসে প্রচলিত ইতিহাসের সাথে সত্যের ব্যাপক বিরোধ দেখতে পান। যা তিনি তার গবেষণায় উল্লেখ করেন।
কোন যুদ্ধেই শুধু একপক্ষের মানুষ মারা যায় না, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের মানুষই মারা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে কোন পক্ষের কত জন নিহত বা আহত হয়েছে তার হিসেব বের করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করেনি বা করতে পারে নি। বাংলাদেশে কত মানুষ মারা গেছে তা নিয়েই কেবল আলোচনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন তার সংখ্যা নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। কারণ এ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হলে যুদ্ধকালে ত্রিশ লাখ মানুষ মারা যাবার তথ্যটি সকলের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোট ৬৬২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে ১৫১১ জন। ৬৬২৯ জনের মধ্যে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১৫৪৪, নৌবাহিনীর সংখ্যা ২১, বিমানবাহিনীর সংখ্যা ৪৭, ইপিআরের সংখ্যা ৮১৭, পুলিশ ১২৬২ আর বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ২৯৩৮ জন নিহত হয়েছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা আমাদেরকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সহায়তা করবে তা হলো, ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকার শহীদ পরিবারকে প্রতিজন শহীদের বিপরীতে ২০০০ (দু’হাজার) টাকা করে অনুদান দেয়ার ঘোষণা করে। সারাদেশ থেকে প্রায় ৭২০০০ আবেদন জমা পড়ে। যাচাই বাছাই করে দেখা যায় এর মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হলো স্বাধীনতাবিরোধী যারা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। পরবর্তীতে রাজাকারদের নাম বাদ দিয়ে করে মোটামুটি ৫০০০০ নিহত ব্যক্তির জন্য তাদের পরিবারকে ২০০০ (দু'হাজার) টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। এই তথ্যকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব স্ট্রাট্রেজিক স্ট্যাডিজের ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসের জার্নালে বলা হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মেয়াদ ছিল ৮ মাস ৩ দিন । এ যুদ্ধে নিহত হয় ৫০ হাজার মানুষ।
উপরে হত্যাকান্ড বা নিহতের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা শুধু পাকিস্তান সামরিকবাহিনী, এর সহযোগী বাহিনী বা দালাল কর্তৃক বাঙালি হত্যার সংখ্যা। এভাবে বিষয়টি একপেশে প্রচারণার শিকার। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী বাঙালি, বিহারি ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী নিহত হওয়ার বিষয়টি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধে পাকিস্তান ও ভারতের সামরিকবাহিনীর সদস্য নিহত হওয়ার বিষয়টিও আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর প্রায় ৪৫০০ সদস্য নিহত ও প্রায় ৮০০০ জন আহত হয়েছেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ১৪২১ সদস্য নিহত ও ৪০৫৮ জন আহত হয়েছে।
বাংলাদেশে একাত্তরে যত নারী-ধর্ষণ হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে সত্যকে ধর্ষণ। গবেষক শর্মিলা বসু তেমনটাই মনে করেন। নারী ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর তার মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে, বাংলাদেশে একাত্তরে নারী ধর্ষণ হয়তো হয়েছে ঠিকই, তবে বিপুল সংখ্যক অবাঙালি মহিলাও বাঙালিদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তার কোনো উল্লেখই নেই। ১৯৭১ সালের ধর্ষণ নিয়ে শর্মিলা বসু তার নিজের গবেষণায় যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হলো, “একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমি দেখলাম, বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীগণ এবং যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারা যুদ্ধের বর্ণনা দিল। গুলি করে হত্যার বর্ণনাও দিল। কিন্তু তারা আমাকে এ কথাও বললো, “আর্মি মহিলাদের কোনো ক্ষতি করেনি। তবে যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় তবে অন্যকথা। একাত্তরে ধর্ষণের যে বিশাল সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে এটি আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আমার কেস স্টাডিজে আমি একটি মাত্র ঘটনারও প্রমাণ পেলাম না।
হত্যার সংখ্যা নিয়ে যেমন অসততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে, ধর্ষণের সংখ্যা নিয়েও তেমনই অসত্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন এই সংখ্যা জরিপ ছাড়াই ছিল দুই লক্ষ। ইতোমধ্যে এক যুগ পরে সেই সংখ্যা আর এক লক্ষ বেড়ে গিয়েছে। এখন বলা হয়, তিন লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই যে প্রচারণা চলছে তারও কোন জরিপ করা হয়নি।
শর্মিলা বসু বলেন “60000 Pakistan Army to kill three million and rape three hundred thousand women, each and everyone of them had to kill 50 persons and rape 5 women.”
শর্মিলা বসু আরো লিখেছেন, //একাত্তরের যুদ্ধের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ২ লাখ থেকে ৪ লাখ ধর্ষিতার যে সংখ্যা বাংলাদেশে বলা হয় তার হিসাব নিকাশের কোন ভিত্তি নেই। এটি অবশ্যই অপ্রত্যাশিত নয় যে ভূক্তভোগীদের সংখ্যার একটি অনুমান (estimate) করা হবে। তবে প্রতিটি অনুমানের মূলেও মাঠ পর্যায়ের কিছু সাক্ষী প্রমাণ থাকতে হয় যার ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান বের করা যায় । কিন্তু বাংলাদেশে একাত্তরে তেমন কিছুই ছিল না। এ ব্যাপারে কোন সরকারি পরিসংখ্যানও নাই। পরিসংখ্যানের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হতে পারতো মাঠপর্যায়ের তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ থেকে। কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া যায় নি।//
(পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল ৬০,০০০; তারা যদি ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে থাকে ও তিন লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করে থাকে , তা হলে প্রতিজন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য গড়ে ৫০ জন মানুষ মেরেছে ও ৫ জন করে মহিলাকে ধর্ষণ করেছে ।)।
ফেরদৌসীর যুক্তি হলো, সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি তাই তাকে খালিশপুরে থাকতে হয়েছিল। তার মতে যেদিন সে প্রথম ধর্ষণের শিকার হয় সেদিন সে তার ম্যানেজারের সাথে দুপুরের খানা খেতে গিয়েছিল, কাজ শেষে সে তার সাথে তার এপার্টমেন্টেও গিয়েছিল। এবং সেখানেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পরের দিন সে আবার কাজে গিয়েছিল। এখানে প্রশ্ন হলো, যে ধর্ষণ নিয়ে একাত্তরের পর সে এতবড় জবানবন্দী পেশ করলো এবং ইতিহাসের বইয়ে প্রকাণ্ড ও একমাত্র সাক্ষীতে পরিণত হলো, অথচ যেদিন সে ধর্ষিতা হলো, সেদিন তার নিজের আচরণটি কেমন ছিল? সে যখন ধর্ষিতা হওয়ার মুখে তখনও সে বাধা দেয়নি। প্রতিবাদও করেনি। ধাক্কাধাক্কি করে সে ধর্ষণ থেকে বাঁচবার বা পলায়নেরও চেষ্টা করেনি। যেখানে ধর্ষণকারি হলো স্বয়ং ম্যানেজার, সে স্থান কোন অবস্থাতেই তার জন্য নিরাপদ ছিল না। অথচ সে বিপদজনক স্থান থেকে সেদিন বা পরের দিন পলায়নও করেনি। পরবর্তী নয় মাসেও সে পলায়নের চেষ্টা করেনি। বরং পরের দিন আবার সে অফিসেই কাজে গেছে। অথচ কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাস করা যাবে না যে ফেরদৌসী বন্দী ছিল। নিরাপদ স্থানে সে চলে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি।//
বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের প্রমাণরূপে খাড়া করা হয়েছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে। শাহরিয়ার কবির তার সম্পাদিত “একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি” বইতে তার জবানবন্দীকে দলিলরূপে পেশ করেছেন। শর্মিলা বসু তার ঘটনা কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে কাজ করছেন। এই বিষয়ে শর্মিলার মন্তব্য হলো, //ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলা এবং পেশায় ভাস্কর। তার কাজের স্থান ছিল খুলনার এক জুটমিলের অফিসে। ফেরদৌসীর অভিযোগ তাকে প্রথমে তার আগাখানী জেনারেল ম্যানেজার ধর্ষণ করে। তারপর সে ১৫ জন পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের নাম নেয় যাদের অবস্থান ছিল যশোর ও খুলনায় । তাদের মধ্য থেকে একমাত্র দুইজন বাদে সবার বিরুদ্ধে হয় ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের চেষ্টা বা অন্য প্রকার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে।
তার নিজের ভাষ্য মতে সে একজন তালাকপ্রাপ্তা তিন সন্তানের মা। তার সন্তানেরা খুলনায় ফেরদৌসীর নানীর কাছে থাকতো আর নিজের মা এবং ৭ জন ভাই-বোন নিয়ে সে খালিশপুরে থাকতো। যেখানে সে জুটমিলে কাজ করতো। আহসান উল্লাহ আহমেদ নামে ফেরদৌসীর একজন পুরুষ বন্ধু ছিল এবং সে ছিল পাশ্ববর্তী আরেকটি জুটমিলের লেবার অফিসার। মিলিটারি এ্যাকশনের পর আহসান উল্লাহ তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলে। ফেরদৌসীর মা এবং তার ভাই-বোনেরাও শহর চলে যায়। তখন ফেরদৌসী একা থেকে যায় তবে মাঝে মধ্যে তার কোন ভাই বা বোন বেড়াতে আসতো। তখন তার পুরুষ প্রেমিকটি পাশেই কাজ করতো।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা মারা গেছেন অথবা তাদের আত্নীয়-স্বজনরা মারা গিয়েছেন এমনটা শুনা যায়নি। শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন “আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোন নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি।” অথচ এর বিপরীতে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়িতেই হত্যা করে। পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের আহবায়ক মৌলভী ফরিদ আহম্মেদকে গুম করা হয়। মুসলিম লীগ নেতা আজিজুল হক চৌধুরী, আব্দুল জব্বার আমীন ও সোলায়মান পাইকারকে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধারা। সাবেক মন্ত্রী জহুরুল হক (লাল মিয়া), সিলেট পিডিপি সভাপতি জসিমউদ্দিন, প্রাক্তন এমএনএ আবদুল হামিদ, মুসলিম লীগ নেতা সিরাজুল হক, বগুড়ার খোরশেদ আলমসহ শত শত স্বাধীনতা বিরোধী নেতা কর্মীকে যুদ্ধ কালেই হত্যা করা হয়। অথচ তারা বেসামরিক নাগরিক ছিলেন। তারা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হন নি।
ধর্ষণের ইতিহাস কীভাবে বিকৃতি করা হয়েছে তার একটি নমুনা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আর জেয়াদ আল মালুমের কথোপকথন থেকেই অনুমান করা যায়। “জেয়াদ আল মালুম বলেন, আমাদের আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের জায়গাটা হলো, সাধারণ ফৌজদারী সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয় থাকে, আমাদের ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের আইনে শুধুমাত্র ব্যক্তি সাক্ষী তাই নয়, এমনও হতে পারে, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, এটাতো নিজেই একটা সাক্ষী। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের একটা অঞ্চলে রেপের ঘটনা রয়েছে। ছাব্বিশাতে বহু রেপ ভিকটিম আছে।
এ সময় কাদের সিদ্দিকী প্রবল আপত্তি তুলে ধরে বলেন, এখানে আমার আপত্তি আছে। ইতিহাস বিকৃত করা অত্যন্ত অন্যায়। ছাব্বিশাতে একটি রেপও হয়নি। ছাব্বিশা মুক্তিযুদ্ধে আমার নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল। ছাব্বিশা গ্রামটি সমস্ত পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিল। তাই আমি বলবো, বিভ্রান্ত করা ভালো কাজ না। এটা বিরক্তিকর। জিয়াদ আল মালুম বলেন, আমি বিভ্রান্ত করছি না। আমাদের কাছে সে ধরনের তথ্য-উপাত্ত আছে। কাদের সিদ্দিকী এ পর্যায়ে বলেন, তথ্য যদি ওই রকম বিভ্রান্তিকর হয় তাহলে তো হবেই। যুদ্ধ করলাম আমি। ছাব্বিশা গ্রামে এক দিনে ৩৬ জন রেপ, যে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হলো, তখন কেউ রেপ করে?”
এখানে যদি জেয়াদ আল মালুম সত্য হয়ে থাকেন তবে ছাব্বিশাতে রেপের ঘটনা কাদেরিয়া বাহিনীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। যা এখন জেয়াদ আল মালুম সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আর যদি কাদের সিদ্দিকী সত্য হয়ে থাকেন তবে সেখানে কোনো রেপের ঘটনা ঘটে নি। জেয়াদ আল মালুম মিথ্যা অভিযোগ করছেন। এখানে জেয়াদ আল মালুম দুই ক্ষেত্রেই মিথ্যেবাদী। কারণ ছাব্বিশাতে একদিন মাত্র অভিযান চালিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী। তাই সেনাবাহিনী দ্বারা রেপের ঘটনা অবাস্তব।
এদেশে প্রকাশ্যে গণহত্যা শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে। যেসব বাঙালি নেতা স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেন নি তাদের বিরুদ্ধে নির্বিচার হত্যা চলতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী ও নিউক্লিয়াসের সদস্যদের দিয়ে গঠিত ভারতীয় জেনারেল ওবানের বিশেষ বাহিনী 'মুজিব বাহিনী'। বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা বিশেষত কওমী মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় সেদিন থেকে। এই হত্যাযজ্ঞ ও গণহত্যা এতই মর্মান্তিক ছিল যে, ঢাকার অনেক কওমী মাদ্রাসা চালু হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগে গিয়েছে।
আর বধ্যভূমির কথা যা বলা হয়েছে তার দিকে যদি আমরা নজর করি তাহলে দেখতে সবগুলো বধ্যভূমি ছিল ভারত থেকে আসা বিহারের মজলুম মুহাজিরদের আবাসস্থলে বা তার কাছাকাছি। বলা যায় এপ্রিল ও মার্চে বিহারীদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্মম ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞই বধ্যভূমির কারণ। যেগুলো এখন বাঙালি হত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইসিটি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জেয়াদ আল মালুমরা এভাবেই তথ্য বিকৃতি করে গেছেন পুরোটা সময় জুড়ে।
এই ১৯৫ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হত্যার নির্দেশের জন্য অভিযুক্ত অর্থাৎ তারা যুদ্ধ করেননি বা সরাসরি অভিযানে যাননি। তাহলে কারা তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করলো? অথবা কারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করলো? ১০০ জনের কম মানুষ কীভাবে লাখ লাখ মানুষকে খুন করলো? এবার আসুন ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে কথা হোক। ১৯৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৩ জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসলো! তাহলে কী এই ১৩ জনই ৩ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করলো! আবার খেয়াল করুন এই ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে মাত্র। প্রমাণিত নয়। যদি অভিযোগ সত্যও প্রমাণিত হয় তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা অনধিক ২০। এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে, কোনো স্থানে ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ পাকিস্তান বাহিনীর সব সদস্যকেই বাঙালি সৈনিকরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তারা চিনতো। একই ক্যান্টনমেন্টেই তারা থাকতো।
১৯৭০ সনের নির্বাচনের পরপরই বিহারিরা নির্যাতিত হতে শুরু করে। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত বিহারিরা দলবদ্ধভাবে থাকা শুরু করে। তারপরও তারা নিজেদেরকে বা পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করতে পারেননি। স্কুল-কলেজ ও কর্মস্থলে যাতায়াতকালে তাদের উপর আক্রমণ হতে শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য স্থানে ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতেই বিহারি ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ও নিউক্লিয়াস। ১৯৭১ সনের ঘটনার ওপর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এসব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ উল্লেখ করা হয়।
এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা থেকে বুঝতেই পারছেন আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে যুদ্ধের হতাহত উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। আর আমি যে অবস্থায় আছি তাতে আমার পক্ষে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা অত্যন্ত বিপদজনক। আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই যা দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন কী পরিমাণ হত্যাকাণ্ড হয়েছে!
সেসময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব বাহিনী মিলে আত্মসমর্পন করেছে ৬০০০০ সেনা ও কর্মকর্তা। ৯৩০০০ হলে বলে যে সংখ্যা আমরা শুনতে পাই তা হলো সেনাবাহিনীর পরিবার পরিজন ও পশ্চিম পাকিস্তানী সাধারণ জনগণসহ। যাই হোক বাংলাদেশ সরকার যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনে তখন স্পেসেফিক নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে পাক সেনাবাহিনীর ৫০০০ এরও বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়। যুদ্ধাপরাধ মানে বেসামরিক মানুষ হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ। এরপর যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশ সরকার এই তালিকা আরো ছোট করে প্রায় ১২০০ জনের তালিকা প্রস্তুত করে। এরপর যখন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করার প্রয়োজন হয় তখন বাংলাদেশ সরকার মাত্র ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে সক্ষম হন। এই ১৯৫ জনকে বিচারের আওতায় আনার কথা ছিল। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় 'শিমলা চুক্তি'র মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার বিপক্ষের মানুষদের বিচার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে শেখ মুজিব সরকার। যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বন্দী সদস্য ও তাদের পরিবার ভারতের জিম্মায় তাই তাদের বিচার ইচ্ছেমত করার সুযোগ ছিল না। তাদের বিচার হবে আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ মামলায়। আর যারা ছিলেন বাঙালি কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী তাদের বিচার করার জন্যে মুজিব সরকার দালাল আইনের ব্যবস্থা করেছিল।
তাহলে এবার বলা যেতে পারে পাকিস্তানীরা নয়, বাঙালিদের মেরেছে ও ধর্ষণ করেছে রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালিরা। সেই চিত্রটাও আমরা একটু দেখে নিতে পারি। এদেশীয় জনগণ যারা স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল তাদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী দালাল আইন প্রণয়নের পর ৬ ফেব্রুয়ারী, ১ জুন ও ২৯ আগস্ট তারিখে তিন দফা সংশোধনীর পর আইনটি চূড়ান্ত হয়।
এ আইনের অধীনে প্রায় একলাখ লোককে আটক করা হয়। এদের মধ্যে থেকে অভিযোগ আনা সম্ভব হয় ৩৭৪৭১ জনের বিরুদ্ধে। বাকীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় ছেড়ে দেয়া হয়। অভিযুক্ত ৩৭৪৭১ জনের মধ্যে থেকে দালালী বা অপরাধের কোন প্রকার প্রমাণ না পাওয়ায় ৩৪৬২৩ জনের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করাই সম্ভব হয়নি। সারাদেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ২২ মাসে বাকি ২৮৪৮ জনকে বিচারের আওতায় আনা হয়।
১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় হয়, ‘যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তারা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।’
যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের বিচার হয়। তাদের মধ্যে বিচারে মাত্র ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বাকী ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। যে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও গুরুদন্ড দেয়ার মতো ছিল না। একজনের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। শুধুমাত্র চিকন আলী নামের একজনকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তাহলে সে আবার আগের প্রশ্ন এত হত্যা কে করলো? এত ধর্ষণ কে করলো?
প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি ২০১০ সাল থেকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা হয়েছে, যারা অভিযুক্ত হয়েছে ও যাদের দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ তো দূরের কথা দালাল আইনেও মামলা করা হয়নি। অথচ তারা প্রকাশ্যে তাদের বাড়িতে, কর্মস্থলে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেছেন। এটা বানোয়াট এবং প্রতিহিংসামূলক বিচার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের অপরাধীদের মধ্যে অবাঙালি হলেন ১৯৫ জন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু বিচার হয়নি। আর বাঙালি অপরাধী হলেন ৭৫২ জন। এই ৭৫২ জনের ১ জন বাদে কেউই হত্যা, গণহত্যা ও ধর্ষণের অপরাধ করেননি বলে বাংলাদেশের আদালত ঘোষণা দিয়েছেন।
যদি সত্যিই অনেক ধর্ষণ হয়ে থাকে অথবা ১০০ টি ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে থাকে তবে এর দায় যুদ্ধের জয়ী পক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর। আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে পুরো বিষয়টাই বানোয়াট ও মিথ্যা।

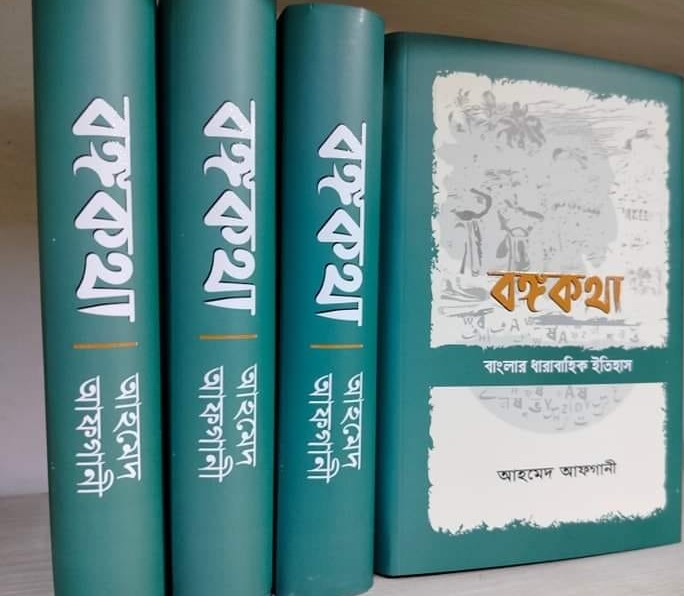





0 comments:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন