স্বাধীনতা পরপরই এদেশের ইসলামপন্থীদের ওপর ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে। এটা অনুমিত ছিল। কারণ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানকে ভাঙতে দিতে চায়নি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম। যারা মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই পাকিস্তান বিভক্তির বিপক্ষে ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধ শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিশেষত কাদের সিদ্দিকীর অধীনে কাদেরিয়া বাহিনী ও জেনারেল ওবানের অধীনে মুজিব বাহিনী। ঢাকা ও তার আশপাশের মুসলিম লীগের নেতা কর্মী, নেজামে ইসলামের নেতা কর্মী, জামায়াতে ইসলামের নেতা-কর্মী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী, ন্যাপের নেতা-কর্মী, মসজিদ্গুলোর ইমাম মুয়াজ্জিন, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্রদের পল্টন ময়দানে জমায়েত করা হতো। তারপর তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হতো। এটা কোনো গোপন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল খুবই প্রকাশ্য এবং দেশি-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে চলে বেসামরিক নাগরিক হত্যা। এদের অপরাধ ছিল তারা পাকিস্তান ভেঙে যাক এটা চায়নি।
একইসাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্ট দখলে নিয়ে সেখানের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সম্পদ লুটপাট করে। এটাও ছিল যুদ্ধাপরাধ। বিরোধী মতের রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ঘর দখল ও লুটপাটের আয়োজন করে মুক্তিবাহিনী। এ সবই ছিল যুদ্ধাপরাধ। যে মুহাজিররা ১৯৪৭ সালে ভারতের বিহার থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলায় এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিবাহিনীর অত্যাচারে আবার ভারতে পাড়ি জমান। এ এক জিল্লতির জীবন ছিল। বিহারীরা ফিরে যেতে পারলেও এদেশের ইসলামপন্থীদের পালানোর জায়গা ছিল না বললেই চলে। সেসময়ের বেশ কয়েকজন ভিকটিমের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা নির্যাতনের মুখে তাদের নিজ জেলা থেকে পালিয়ে দূরের জেলায় পালিয়ে থেকেছে।
ইসলামের প্রতি আক্রোশ :
শুধু যে ইসলামপন্থীরা আক্রান্ত হয়েছে তা নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ইসলাম বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা ইসলামের প্রতি আক্রোশ দেখিয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নামে ইসলাম ও মুসলিম ছিল সেগুলো থেকে তারা ইসলাম ও মুসলিম শব্দ বাদ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম বাদ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো থেকে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' ও কুরআনের চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম বাদ দিয়েছে। পাবনার সেরা কলেজ ইসলামিয়া কলেজকে বুলবুল কলেজে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে সারা বাংলাদেশে সব স্থান ইসলাম ও মুসলিমকে উৎখাত করা হয়েছে। কওমী মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বোরকা নিষিদ্ধ করে শাড়ি পড়তে বাধ্য করা হয়েছে। এই কারনে বহু ছাত্রী একাত্তর পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে যায় নি।
সংবিধান প্রণয়ন করে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, নেজামী ইসলামী ও জামায়াতে ইসলামী এই দুইদলই ছিল সেসময় ইসলামী রাজনীতির ধারক ও বাহক। এদের নিষিদ্ধ করা হয় নাই যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। বরং তাদের এইজন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাজনীতি করেন। সেসময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী ন্যাপ (মুজাফফর), মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি এবং কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল এই দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের যারা কুশীলব তাদের মূল আক্রোশ ছিল ইসলামের সাথে। এই সাধারণ ব্যাপার সেসময়ের সকল ইসলামী রাজনীতিবিদ বুঝেছিলেন এবং তারা এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। সেসময়ের অনেক মুসলিম না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো এটা তাদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করুন।
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা রেডিও টেলিভিশনে বিসমিল্লাহ, সালাম দিয়ে শুরু করা বাদ দিয়ে সুপ্রভাত, শুভকামনা ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করেছে। রেডিওতে কুরআন তিলওয়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী একাডেমি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ইসলামী একাডেমীকেই তিনবছর পরে ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে চালু করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আবার পুনরায় রেডিও টেলিভিশনে সালাম, বিসমিল্লাহ, আযান ও কুরআন তেলওয়াত শুরু হয়েছিল।
এইসব কাজ শেখ মুজিব তার নিজস্ব পরিকল্পনাতে করেছেন এটা আমি বলতে চাই না। মুজিব পরিবেষ্টিত ছিলেন তাজউদ্দিনদের মতো এক ঝাঁক কমিউনিস্ট দ্বারা। তার ফলে মুজিবের শাসনামলের শুরুর দিকে সমস্ত ইসলামবিরোধী কাজের জোয়ার শুরু হয়েছিল। সংবিধান থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাদ পড়েছে। মূলনীতি থেকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস বাদ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কমিউনিজম, সেক্যুলারিজমের মতো ইসলাম ও ধর্ম বিদ্বেষী মতবাদকে। ক্ষমতায় থেকে ইসলামপন্থা দমনে সব কাজ করেছেন শেখ মুজিব। যখন জাসদ গঠিত হয় এবং বামপন্থীদের সাথে সরকারের চরম বিরোধ শুরু হয় তখন মুজিব কোনঠাসা হয়ে থাকা ইসলামপন্থীদের কাছে টানতে থাকেন তার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। তবে অবশ্যই তিনি ইসলামী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি শুধুমাত্র অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিয়েছেন। তাবলীগের প্রসার করার চেষ্টা করেছেন। কওমীদের শুধুমাত্র মাদ্রাসার গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।
জাতীয়করণ :
কমিউনিজমের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে একের পর এক শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেন মুজিব। তবে কোনো বাঙালির কারখানা জাতীয়করণের আওতায় আসে নি। ১৯৪৭ এর পর বাঙালি রাজনীতিবিদেরা সবসময় মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাতেন এদেশে ব্যবসা করার জন্য, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাতে সাড়া দেয় অনেক অবাঙালি কোম্পানি। এরা বেশির ভাগ ভারত ও মিয়ানমারের। এর মধ্যে বড় ব্যাবসায়ি গোষ্ঠী ছিল আদমজি, বাওয়ানী ও ইস্পাহানী পরিবার। এর বাইরেও বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এদেশে এসেছিলেন। বাংলা ও বাঙালির উন্নয়নে এসব উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেক অবদান ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব জাতীয়করণের নামে এসব অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সমস্ত সম্পদ ও কারখানা দখল করে নেয়। যারা এতদিন এদেশের নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের উন্নয়নে ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রেখেছিল শেখ মুজিব তাদের রিক্ত হস্তে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। তবে দুঃখজনক হলো, এসব শিল্প কারখানা থেকে বাংলাদেশ কখনোই লাভবান হতে পারে নি। সরকার বছর বছর কেবল এগুলোতে ভর্তুকি দিয়েই আসছে।
লুটপাট :
যুদ্ধপরবর্তী মানুষের পুনর্বাসন একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মুজিব সরকারের জন্য। সেজন্য মুজিব জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশাল ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের লুটেরা গোষ্ঠীর লুটপাটে এই ত্রাণ থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের এতো উর্ধ্বগতি হয়েছিল যে, লবণের কেজি ৯০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। অথচ যুদ্ধের সময়ও ১ মণ চাউলের দাম ছিল ১৫-২০ টাকা। মুজিবের আমলে চাউলের কেজি ১০০-১৬০ টাকা, মশুর ডাল ১২০-১৫০ ও সয়াবিন ৫৯০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে। এর বড় কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধারা আমদানিকৃত দ্রব্য আটকে দাম বাড়াতো, একইসাথে এদেশীয় কৃষকের ক্ষেতের ফসলও তারা লুটপাট করে নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। ১৯৭০ সালে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' বলে মিথ্যা প্রচারণাকারীরা টের পেল সোনার বাংলা কীভাবে মুজিবের হাতে শ্মশান হয়!
রক্ষিবাহিনী :
মুজিব তার একান্ত অনুগত একটি বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এটা অনেকটা জার্মানীর গেস্টাপো বাহিনীর মতো ছিল। সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাপরাধ করা কাদেরিয়া ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে মুজিব তার সমস্ত পরিকল্পনা মুহুর্তেই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। একইসাথে বিরোধী মত দমনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে রক্ষিবাহিনী। মূলত পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আদর্শের লোক থাকায় সেসব বাহিনীর ওপর মুজিব ভরসা করতে পারেননি। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এই বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, গুম, গোলাগুলি, লুটপাট এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ঝটিকা বাহিনীর মতো রক্ষীবাহিনী প্রায়ই একেকটি গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং অস্ত্র ও দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজতো।
তাদের নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে লুটপাট এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগও ছিল। তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা যখন তুঙ্গে ওঠে এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তখন ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৭৩ জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে। রক্ষীবাহিনীর কোন সদস্য সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করলে অথবা সৎ উদ্দেশ্যে উক্ত কাজ করে থাকলে অনুরূপ কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া যাবে না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এই বাহিনীকে বিরুদ্ধ মত ও জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন শেখ মুজিব। রক্ষিবাহিনীর সাথে সরাসরি বিরোধ তৈরি হয় সেনাবাহিনীর সাথে। এই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি হতো।
লালবাহিনী :
রক্ষীবাহিনী যেভাবে সরকারের ঘোষিত বাহিনী ছিল লালবাহিনী সেভাবে সরকারি বাহিনী ছিল না। আওয়ামী লীগের মধ্যে বামপন্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে ছিল। বামদের বড় অংশ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে। যখন আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা বামপন্থীরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে আলাদা হয়ে যায় তখন বাকীরা আওয়ামী শ্রমিক লীগ নামধারণ করে। যেহেতু জাসদের বড় অংশ ছিল শ্রমিক তাই শেখ মুজিব জাসদকে কন্ট্রোল করার জন্য শ্রমিক লীগকেই বেছে নিয়েছেন।
আবদুল মান্নান, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রধান ছিলেন, তার নেতৃত্বেই লালবাহিনী গঠন করা হয়। এটি ছিল একটি সশস্ত্রবাহিনী। এটিও সরকারের আজ্ঞাবহ তবে সরকার এর দায়দায়িত্ব নিত না। তাদের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করা। শ্রমিকদের মধ্যে জাসদের কার্যক্রম বন্ধ করাও ছিল লালবাহিনীর কাজ। ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে অবাঙালিদের কারখানাগুলিকে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণার পরে লাল বাহিনী তাদের 'বিরোধী দল' হিসেবে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য শুদ্ধি অভিযান শুরু করে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে লাল বাহিনীর শুদ্ধি অভিযানের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তথাকথিত শোষণকারীদের শেষ করতে তাঁর 'লাল ঘোড়া' মোতায়েনের হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভাষণে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেওয়া হবে হুমকি দিতেন। লালবাহিনীর প্রধান আবদুল মান্নানকে এমনও বলতে শোনা গেছে যে, "নতুন ফ্রন্ট (জাসদের শ্রমিক ফ্রন্ট) যদি মুজিববাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে তবে আমি তাদের জিহ্বা কেটে দেব"।
লাল বাহিনীর গণহত্যা :
লাল বাহিনীর প্রথম নৃশংসতা করেছিল মংলা বন্দরে। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কুলি হিসাবে কাজ করত। ধারণা করা হয়েছিল যে বামপন্থী শ্রমিক মোর্চা ও বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের মধ্যে কুলিদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব থেকেই এই গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসারে দাঙ্গার ফলে প্রায় ৩৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তবে প্রকৃত মৃত্যুর হার সরকার কর্তৃক বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দাঙ্গা চলাকালীন বাংলাদেশে থাকা বিশিষ্ট সাংবাদিক মাসকারেনহাসের মতে, সেদিন প্রায় ২০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং তারা সবাই বামপন্থী শ্রমিক ছিল। এই ঘটনা স্বাধীনতার কিছু দিন পর ১৯৭২ সালের মার্চে সংঘটিত হয়।
আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা ছিল ৫ এপ্রিল। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মীদের উপর লাল বাহিনীর লোকেরা হামলা করে। এই হামলার লক্ষ্য ছিল টঙ্গীর ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থিত ফেডারেশন কর্মীদের প্রভাব শেষ করা। ঐ সময় বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এটি বৃহত্তম ছিল। লাল বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় হাজার হাজার শ্রমিক নির্যাতিত ও সহিংসতার শিকার হয়। ন্যাপের দাবি অনুসারে সেখানে শতাধিক শ্রমিক খুন হন।
কালুরঘাট শিল্পাঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের আরআর জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলের দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী ছিল এই লালবাহিনী। এই দাঙ্গার পেছনের প্রধান কারণ ছিল 'স্থানীয় ও অ-স্থানীয় সমস্যা' এবং 'জেলাবাদ' যা লালবাহিনী সদস্যরা প্রবর্তন করেছিল এবং এটি শ্রমিকদের পার্থক্য করতে ব্যবহৃত হত। চট্টগ্রাম যেহেতু একটি বন্দর নগরী ছিল তাই অন্যান্য জেলা থেকে কাজের সন্ধানে অনেক শ্রমিককে চট্টগ্রাম আসতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের মে মাসে লাল বাহিনী সদস্যরা স্থানীয়-অ-স্থানীয় সমস্যাটি ব্যবহার করে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছিল। যেভাবে আগে তারা বামপন্থী ইস্যুতে শুদ্ধি অভিযান করেছিল। এই হামলায় চট্টগ্রামে কাজ করতে আসা শত শত শ্রমিককে খুন করে লালবাহিনী।আরো বেশ কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল এবং খুনোখুনি ছিল নিয়মিত ঘটনা। এতে মিলগুলির উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছিল। লালবাহিনীর দৌরাত্মে কারখানাগুলো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়েছিল। কারখানাগুলোর শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলো। লালবাহিনীর অশিক্ষিত শ্রমিকরাই তাদের ইচ্ছেমতো কারাখানা পরিচালনা করতে লাগলো। এরপর সরকার একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি।
ভারতের আজ্ঞাবহ :
শেখ মুজিব সরকার ভারতের আজ্ঞাবহ সরকারে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতো না। পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিটা সিদ্ধান্তের জন্য ভারতের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে মুজিবকে। শেখ মুজিব তার ক্ষমতার শেষদিকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। তদুপরি সে যখন দেখলো সে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে, দুর্ভিক্ষ ছাড়ছেই না। জনগণ বেকার হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেছে তখন শেখ মুজিব তার নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। তিনি তার বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া, কিউবা, ভারত, ইংল্যান্ড থেকে সরে এসে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে বন্ধুত্বের অনুরোধ নিয়ে ছোটাছুটি করলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শুভদৃষ্টি পেতে চাইলেন। ৭৪-এ আলজেরিয়াকে মিডিয়া বানিয়ে কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার শর্তে বাংলাদেশ ওআইসির স্বীকৃতি লাভ করে। এর পরপরই তিনি পাকিস্তানে ওআইসি'র সম্মেলনে যোগ দেন। এই ঘটনায় ভারতের সাথে শেখ মুজিবের দূরত্ব তৈরি হয়।
বাকশাল :
শেখ মুজিব তার ক্ষমতার একেবারে শেষদিকে এসে মাও সে তুং-এর মতো করে একদলীয় শাসন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে শুধু একটি দল থাকবে তার নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুসারে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমগ্র রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামক এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। বাকশাল ব্যবস্থায় দলের চেয়ারম্যানই সর্বক্ষমতার অধিকারী। চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন এবং একমাত্র চেয়ারম্যানই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করতে পারবেন।
বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে কোন নির্দলীয় শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক সংগঠন এবং গণসংগঠন করার কোন অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়ন মাত্রই তাকে বাকশালের অঙ্গদল শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই ব্যবস্থায় জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুবলীগ এবং জাতীয় ছাত্রলীগ বাদে কোন শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব ও ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না। আর উপরিউক্ত সংগঠনগুলি হচ্ছে বাকশালেরই অঙ্গ সংগঠন। বাকশাল আইনের অধীনে ১৯৭৫ সালের ৬ জুন দেশে চারটি দৈনিক ছাড়া আর সকল সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। ঐ চারটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার।

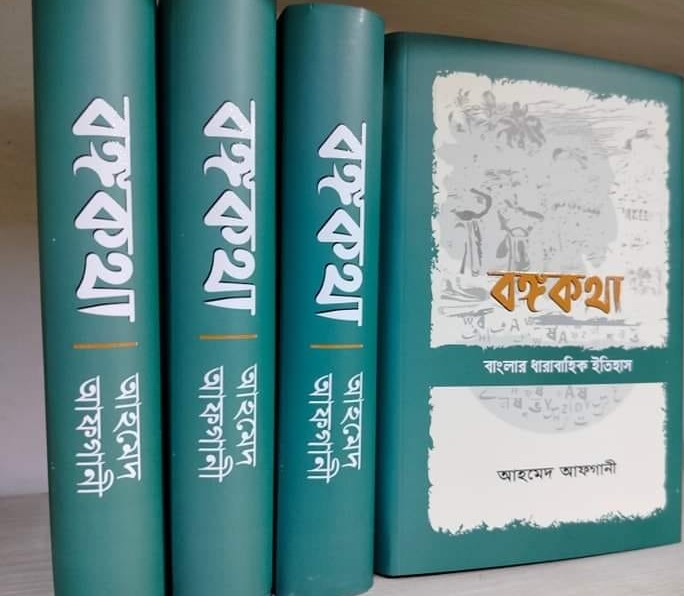





0 comments:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন